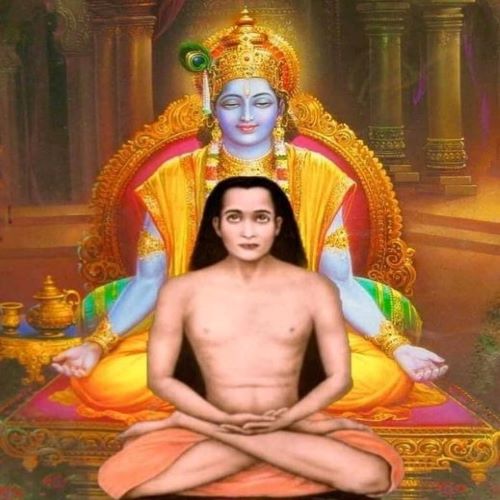
ভারতেমোট 192 টি তন্ত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে
ভারতেমোট 192 টি তন্ত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সকল তন্ত্রকে 64 করে মোট তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা
1. বিষ্ণুক্রান্তা
2. অশ্বক্রান্তা
3.রথক্রান্তা।
বিষ্ণুক্রান্তা
পশ্চিমবঙ্গ বিষ্ণুক্রান্তার অন্তর্ভুক্ত। এই ক্রান্তার অন্তর্গত ৬৪ প্রকার তন্ত্রের বেশিরভাগ লুপ্ত প্রায়।
এই ৬৪ প্রকার তন্ত্রসমূহ হল নিম্নরূপ
১)কালী তন্ত্র
২)তারা তন্ত্র
৩)শিবসার তন্ত্র
৪) মহানির্বাণ তন্ত্র
৫) মুণ্ডমালা তন্ত্র
৬)তোড়ল তন্ত্র
৭) লিঙ্গার্চন তন্ত্র
৮) রাধা তন্ত্র
৯)লতার্চন তন্ত্র
১০)বিশ্বসার তন্ত্র
১১)নীল পতাকা তন্ত্র
১২)অকুল বীর তন্ত্র
১৩)মাতৃভেদ তন্ত্র
১৪) ভৈরবী তন্ত্র
১৫)গুপ্তসাধন তন্ত্র
১৬)ভৈরবজামল তন্ত্র
১৭) সময়াচার তন্ত্র
১৮) মায়া তন্ত্র
১৯)চিদাম্বর সংহিতা তন্ত্র
২০) সিদ্ধেশ্বর তন্ত্র
২১)মহামায়া তন্ত্র
২২)কালিকাকূল তন্ত্র
২৩)অক্ষয়া তন্ত্র
২৪) কুলার্ণব তন্ত্র
২৫) কালিকাকল্প তন্ত্র
২৬) কুমারীকল্প তন্ত্র
২৭)যোগিনী তন্ত্র
২৮) বারাহী তন্ত্র
২৯) ত্রিপুরাসার তন্ত্র
৩০) যোগিনী হৃদয় তন্ত্র
৩১)সনৎ কুমার তন্ত্র
৩২) মালিনী বিজয় তন্ত্র
৩৩)কুক্কুট তন্ত্র
৩৪)গণেশ বিমর্ষিনী তন্ত্র
৩৫) ভূতডামর তন্ত্র
৩৬) যোগিনী বিজয়া তন্ত্র
৩৭) উডডীশ তন্ত্র
৩৮) বীরভদ্র তন্ত্র
৩৯)বরদা তন্ত্র
৪০) কামধেনু তন্ত্র
৪১)বামকেশর তন্ত্র
৪২) জ্ঞানার্ণব তন্ত্র
৪৩) ভাবচূড়ামণি তন্ত্র
৪৪)কালিকাবিলাস তন্ত্র
৪৫) তট তন্ত্র
৪৬) হংস মাহেশ্বর তন্ত্র
৪৭)চিদাম্বর তন্ত্র
৪৮) বিজ্ঞাপন তন্ত্র
৪৯) তন্ত্র চিন্তামণি
৫০) কুলচূড়ামণি তন্ত্র
৫১)ফেৎকারিনী তন্ত্র
৫২)নারায়নী তন্ত্র
৫৩) কামাখ্যা তন্ত্র ( গুহ্যসিদ্ধি)
৫৪) স্বতন্ত্র তন্ত্র
৫৫) যোনি তন্ত্র
৫৬) মন্ত্র মুক্তাবলী তন্ত্র
৫৭) গন্ধর্ব তন্ত্র
৫৮) কুব্জিকা তন্ত্র
৫৯) বৃহৎ শ্রীক্রম তন্ত্র
৬০) গৌতমীয় তন্ত্র
৬১) নিরুত্তর তন্ত্র
৬২) জ্ঞানদীপ তন্ত্র
৬৩) নিত্যোৎসব তন্ত্র
৬৪)উদ্ধাম্মায় তন্ত্র
****************************************************************************************************
অশ্বক্রান্তা
মোট ১৯২টি তন্ত্রের মধ্যে অশ্বক্রান্তার অন্তর্গত হল ৬৪টি তন্ত্র। বিন্ধ্য পর্বত থেকে ভারতের দক্ষিণাংশ অশ্বক্রান্তার অন্তর্গত। এর অন্তর্গত তন্ত্রসমূহ হল
১) বৃহৎতোড়ল তন্ত্র
২) কাল তন্ত্র
৩) গৌরী তন্ত্র
৪) কামিনী তন্ত্র
৫) মোহিনী তন্ত্র
৬) যোগ তন্ত্র
৭) বিন্দু তন্ত্র
৮) শিব তন্ত্র
৯) সিদ্ধ তন্ত্র
১০) বর্ণসার তন্ত্র
১১) ক্রিয়াসার তন্ত্র
১২) বৃহৎসার তন্ত্র
১৩) গুপ্তদীক্ষা তন্ত্র
১৪) ভূতশুদ্ধি তন্ত্র
১৫) তত্ত্বসার তন্ত্র
১৬) ধর্মক তন্ত্র
১৭) গুপ্তসার তন্ত্র
১৮) গুপ্ত তন্ত্র
১৯) তত্ত্বচিন্তামণি তন্ত্র
২০) মহাযোগিনী তন্ত্র
২১) শূলিনী তন্ত্র
২২) বৃহদ্ - যোগিনী তন্ত্র
২৩)সম্বর তন্ত্র
২৪) শিবাঞ্জন তন্ত্র
২৫) বৃহৎকঙ্কালিনী তন্ত্র
২৬) বৃহন্নির্বাণ তন্ত্র
২৭) মোক্ষ তন্ত্র
২৮) মহামোক্ষ তন্ত্র
২৯) মহামালিনী তন্ত্র
৩০) গোপী তন্ত্র
৩১) বৃহন্মালিনী তন্ত্র
৩২) ভূতলিপি তন্ত্র
৩৩) মোহন তন্ত্র
৩৪) বৃহন্মোক্ষ তন্ত্র
৩৫) কামকেশর তন্ত্র
৩৬) সমীরণ তন্ত্র
৩৭) মহাবীর তন্ত্র
৩৮) চূড়ামণি তন্ত্র
৩৯) গুর্বর্চ্ছন তন্ত্র
৪০)গোপ্যা তন্ত্র
৪১) মঙ্গলা তন্ত্র
৪২) তীক্ষ্ণ তন্ত্র
৪৩) কামরত্ন তন্ত্র
৪৪) ব্রহ্মাণ্ড তন্ত্র
৪৫) গোপলীলা তন্ত্র
৪৬) চীন তন্ত্র
৪৭) মহানিরুত্তর তন্ত্র
৪৮) ভূতেশ্বর তন্ত্র
৪৯) গায়ত্রী তন্ত্র
৫০)যোহার্ণব তন্ত্র
৫১) সারাৎসার তন্ত্র
৫২) বিশুদ্ধেশ্বর তন্ত্র
৫৩) শিবাতন্ত্র
৫৪) ধূমাবতী তন্ত্র
৫৫) উজ্জাসক তন্ত্র
৫৬)মন্ত্রচূড়ামণি তন্ত্র
৫৭) যন্ত্রচূড়ামণি তন্ত্র
৫৮) ভেরুণ্ডা তন্ত্র
৫৯) লীলাবতী তন্ত্র
৬০) ভুবনেশ্বরী তন্ত্র
৬১)বিদ্যুল্লতা তন্ত্র
৬২) বৃহচ্ছীন তন্ত্র
৬৩)জয় রাধামাধব তন্ত্র
৬৪) কুরঞ্জ তন্ত্র
উপরোক্ত অধিকাংশ তন্ত্র বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায় ও এদের প্রয়োগও খুবই কম।
*****************************************************************************************************************
রথক্রান্তা
মোট ১৯২টি তন্ত্রের মধ্যে রথক্রান্তার অন্তর্গত তন্ত্রসমূহের সংখ্যা ৬৪টি। উত্তরপূর্ব ভারত তথা তিব্বতের বেশ কিছুস্থান রথক্রান্তার অন্তর্গত। এর অন্তর্গত তন্ত্রসমূহের নাম হল-
১)শক্তিবিলাস তন্ত্র
২) হংস তন্ত্র
৩) মহাডামর তন্ত্র
৪)মহিষমর্দিনী তন্ত্র
৫)চিন্ময় তন্ত্র
৬)মাতৃকোদয় তন্ত্র
৭) মেরু তন্ত্র
৮)একজটা তন্ত্র
৯) মহানীল তন্ত্র
১০) দেবডামর তন্ত্র
১১) মৎস্যসূক্ত তন্ত্র
১২) বাসুদেব রহস্য তন্ত্র
১৩) বৃহদগৌতমীয় তন্ত্র
১৪)বীজচিন্তামণি তন্ত্র
১৫)ছায়ানীল তন্ত্র
১৬)বৃহদযোনি তন্ত্র
১৭)বালা- বিলাস তন্ত্র
১৮)গারুড় তন্ত্র
১৯)বর্ণ-বিলাস তন্ত্র
২০)ব্রহ্মজ্ঞান তন্ত্র
২১) পরমেশ্বর তন্ত্র
২২) প্রপঞ্চসারতন্ত্র
২৩) পিচ্ছিলা তন্ত্র
২৪)ভূতভৈরব তন্ত্র
২৫)কালভৈরব তন্ত্র
২৬)শারদা তন্ত্র
২৭) পঞ্চদশী তন্ত্র
২৮) যোগসার তন্ত্র
২৯) মহালক্ষ্মী তন্ত্র
৩০) কৈবল্য তন্ত্র
৩১)কৃতিসার তন্ত্র
৩২) শক্তিসঙ্গম তন্ত্র
৩৩)নারদীয় তন্ত্র
৩৪) উদ্দামরেশ্বর তন্ত্র
৩৫)সিদ্ধিতদ্ধরী তন্ত্র
৩৬)ষাড়ান্মায় তন্ত্র
৩৮)কুলসদ্ভাব তন্ত্র
৩৯)চীনাচার তন্ত্র
৪০)করালভৈরব তন্ত্র
৪১) সোঢ়া তন্ত্র
৪২)সরস্বতী তন্ত্র
৪৩) যক্ষডামর তন্ত্র
৪৪) আচারসার তন্ত্র
৪৫) সন্মোহিনী তন্ত্র
৪৬)কালোত্তম তন্ত্র
৪৭) পুরশ্চরণ- রসোল্লাস তন্ত্র
৪৮) ইন্দ্রজাল তন্ত্র
৪৯) কঙ্কালমালিনী তন্ত্র
৫০) রেবতী তন্ত্র
৫১) রাজরাজেশ্বরী তন্ত্র
৫২) দক্ষিণামূর্তি তন্ত্র
৫৩) আকাশভৈরব তন্ত্র
৫৪) যক্ষিণী তন্ত্র
৫৫) নবরত্বেশ্বর তন্ত্র
৫৬) পুরশ্চরণ- চন্দ্রিকা তন্ত্র
৫৭) নাগার্জুন তন্ত্র
৫৮) সারস তন্ত্র
৫৯) জ্ঞানভৈরব তন্ত্র
৬০) স্বরোদয় তন্ত্র
৬১)শক্তিকাগমসর্বস্ব তন্ত্র
৬২)কৃকলাস- দীপিকা তন্ত্র
৬৩) যোগ - স্বরোদয় তন্ত্র
৬৪)বর্ণ-ধৃতি তন্ত্র
উল্লিখিত অধিকাংশ তন্ত্র ও তাদের প্রয়োগ বর্তমানে বিলুপ্ত প্রায়।
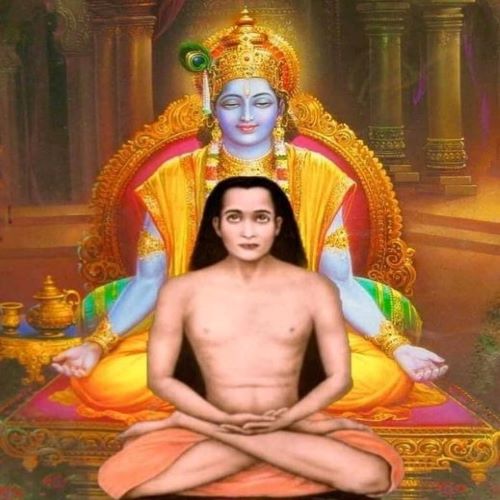
অগ্নি পুরাণ
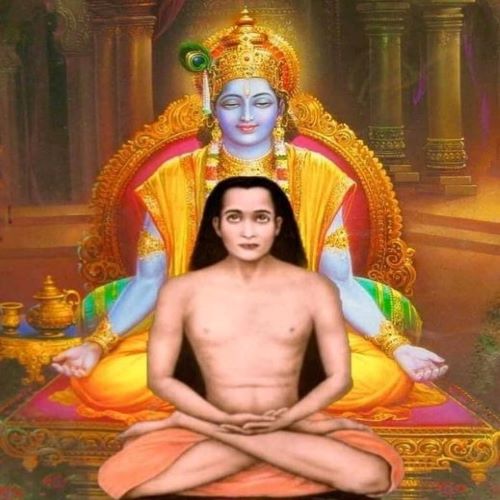
গরুড় পুরাণ
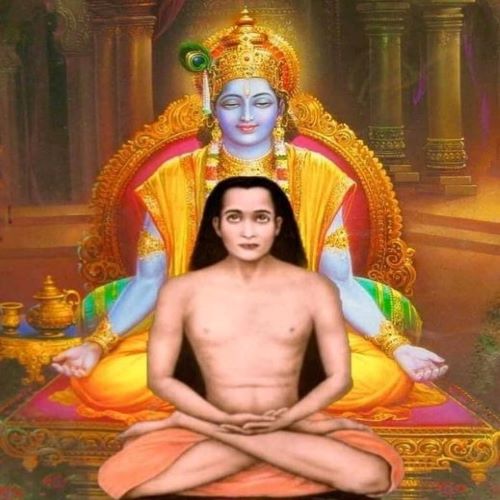
মহাভারতে সঞ্জয় কে ছিলেন ?
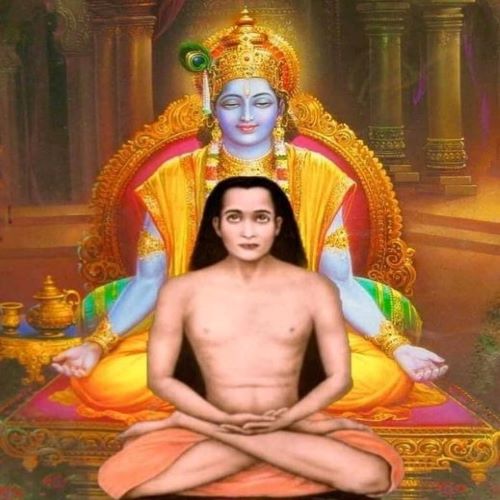

ব্রহ্ম সংহিতা
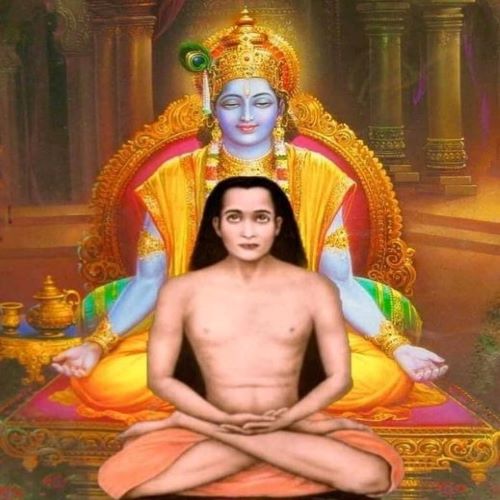
উপনিষদ হল পবিত্র ধর্মগ্রন্থ
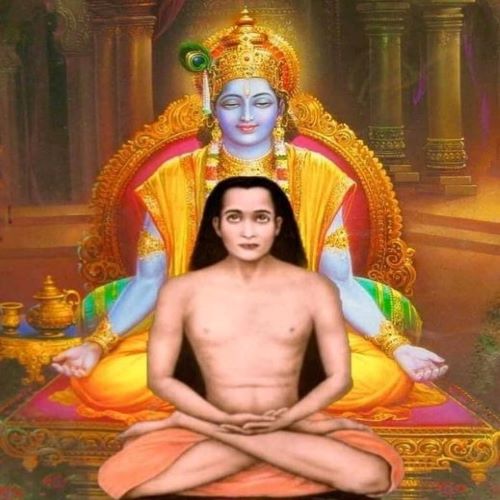

শ্লোক বৃহদারণ্যক উপনিষদ
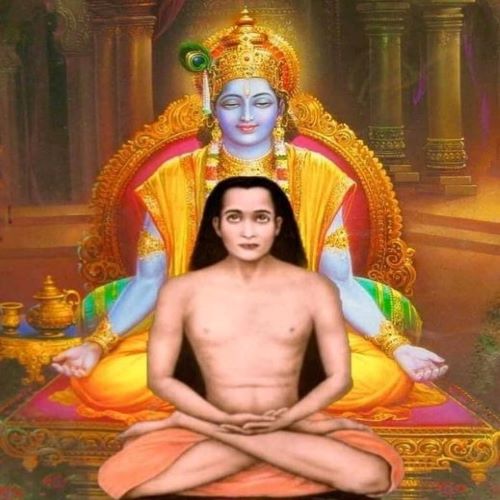

কঠোপনিষদ্ / তৃতীয়া বল্লী / চতুর্দশতম শ্লোক
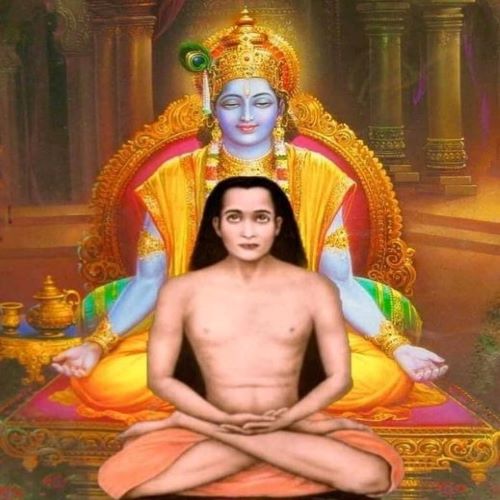

বেদ কী?
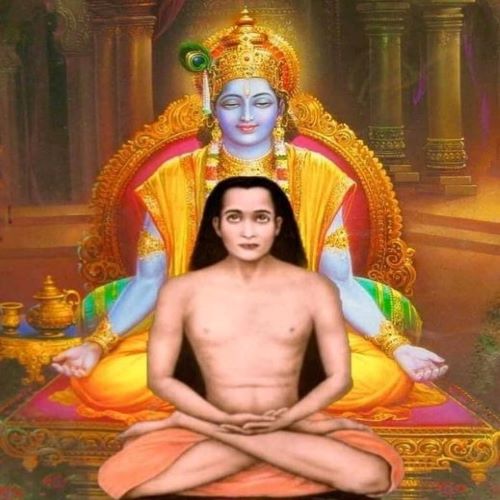

194 খানি তন্ত্র শাস্ত্রের প্রকারভেদ
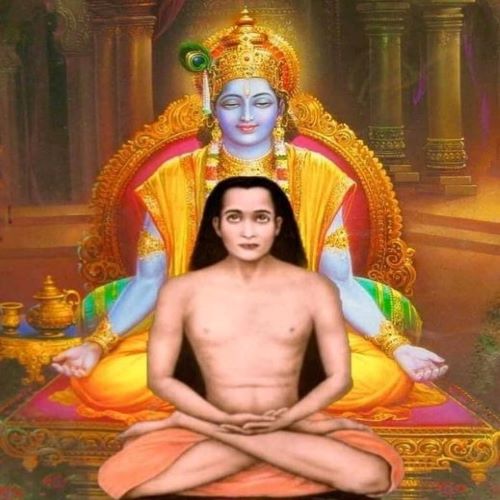
মহাভারতে উল্লেখিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরবর্তী রাজাদের তালিকা
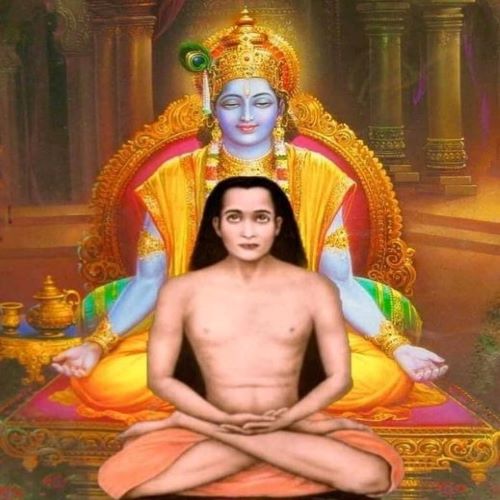

মহাভারত
